ঘরোয়া মাটিতে সেনা মোতায়েনের পক্ষে ট্রাম্পের জোর প্রচারণা
ভূমিকা
অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, সহিংস বিক্ষোভ এবং নির্বাচনের পরবর্তী পরিস্থিতি ঘিরে ইতোমধ্যেই ট্রাম্প নিজেকে ‘আইন-শৃঙ্খলার রক্ষক’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই প্রেক্ষাপটে ‘ইনসারেকশন অ্যাক্ট’ নিয়ে তার বারবার মন্তব্য এবং পরোক্ষ হুমকিকে বিশেষজ্ঞরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ওপর বড় ধরণের হুমকি বলে মনে করছেন।
ইনসারেকশন অ্যাক্ট কী?
‘ইনসারেকশন অ্যাক্ট’ (Insurrection Act) মার্কিন কংগ্রেস কর্তৃক ১৮০৭ সালে পাস হওয়া একটি আইন, যার মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট জরুরি পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনী বা ন্যাশনাল গার্ডকে দেশের অভ্যন্তরে মোতায়েন করতে পারেন। এটি মূলত বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ, দাঙ্গা, বা আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটলে কার্যকর হয়।
আইনটির উদ্দেশ্য ছিল ফেডারেল সরকার যখন রাজ্য সরকার বা স্থানীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ ব্যর্থ হয়, তখন রাষ্ট্রপতির হাতে ক্ষমতা দেওয়া। তবে যুগে যুগে এই আইনের প্রয়োগ নিয়ে প্রশ্ন ও বিতর্ক তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে এটি কতটা গণতন্ত্র-বান্ধব, তা নিয়ে।
ট্রাম্পের অবস্থান ও বক্তব্য
ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি একাধিক জনসভা, টিভি সাক্ষাৎকার এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বারবার এই আইনের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। তিনি দাবি করছেন, যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে “আইনহীনতার চরম পর্যায়ে” রয়েছে, যেখানে সহিংসতা, অভিবাসী সঙ্কট, মাদক চোরাচালান এবং বর্ণগত বিভাজন দ্রুত বাড়ছে। এই প্রেক্ষাপটে, রাষ্ট্রপতির হাতে “শক্তি প্রয়োগের পূর্ণ অধিকার থাকা উচিত” বলেই তিনি মত প্রকাশ করেছেন।
ট্রাম্প বলেন:
“যদি দেশের অভ্যন্তরে আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে, তাহলে আমাদের শক্ত হাতে হস্তক্ষেপ করতে হবে। আমার প্রশাসন সেটা করবে, সেনাবাহিনীকে প্রয়োজনে ব্যবহার করব।”
তিনি দাবি করছেন, রাষ্ট্রের ভেতরে “গণতান্ত্রিক ভান করে অনাচার চালানো হচ্ছে,” যা শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপেই বন্ধ হতে পারে।
২০২০ সালের অভিজ্ঞতা এবং পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা
ট্রাম্প এর আগে ২০২০ সালে জর্জ ফ্লয়েড হত্যাকাণ্ডের পর দেশজুড়ে বর্ণবৈষম্যবিরোধী বিক্ষোভের সময়ও ইনসারেকশন অ্যাক্ট প্রয়োগের কথা বলেন। যদিও সেসময় সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ নেতারা বিরোধিতা করেন এবং আইনটি কার্যকর হয়নি, তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে ট্রাম্প আরও সুসংগঠিতভাবে আইনের প্রয়োগের পক্ষে অবস্থান নিচ্ছেন।
বিশ্লেষকদের মতে, এবার তিনি আগেই ‘আইনি ভিত্তি’ তৈরি করে নিচ্ছেন, যাতে নির্বাচনের পর কোনোরকম বিশৃঙ্খলা ঘটলে, তৎক্ষণাৎ সেনা মোতায়েন করা যায়।
নির্বাচনের পটভূমিতে সেনা মোতায়েনের বার্তা
ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২৪ সালের নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রধান প্রার্থী। নির্বাচনী প্রচারণার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে ‘আইন ও শৃঙ্খলা’। ট্রাম্প চান, নিজেকে এমন একজন নেতারূপে প্রতিষ্ঠা করতে যিনি “দমনমূলক নীতির মাধ্যমে দেশকে স্থিতিশীল রাখতে পারবেন।”
এভাবে সেনা মোতায়েনের বার্তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করছেন ট্রাম্প, যেন তিনি ক্ষমতায় ফিরলে “সিস্টেম ক্লিন” করার মতো একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি হবেন।
বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা: গণতন্ত্রের উপর আঘাত
যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক সাংবিধানিক আইনবিদ, অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক এ বিষয়ে তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক লরেন্স স্যামুয়েল বলেন,
“ট্রাম্প ইনসারেকশন অ্যাক্টকে রাজনৈতিক হাতিয়ার বানাতে চাইছেন। তিনি যদি সেনাবাহিনী ব্যবহার করে অভ্যন্তরীণ বিরোধ বা বিক্ষোভ দমন করেন, তাহলে এটি একটি কার্যত স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠার সূচনা হবে।”
অনেকেই মনে করছেন, সেনাবাহিনীকে এমনভাবে দেশের জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহারের মানে হলো আমেরিকার গণতন্ত্র, নাগরিক অধিকার এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার সরাসরি লঙ্ঘন।
সেনা কর্মকর্তাদের প্রতিক্রিয়া
অবসরপ্রাপ্ত বেশ কিছু জেনারেল এবং ন্যাশনাল গার্ড কমান্ডার এই প্রস্তাবনার বিরোধিতা করেছেন। তাদের মতে, সেনাবাহিনী দেশের জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়। সেনাবাহিনী অভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রাখার জন্য নয়, বরং বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রতিষ্ঠিত।
সাবেক সেনাপ্রধান মার্ক মিলি ২০২০ সালে বলেছিলেন, “সেনাবাহিনী রাজনীতির অংশ নয়, এবং অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে আমাদের ব্যবহারের চেষ্টা করা হবে বড় ভুল।”
সামাজিক প্রতিক্রিয়া ও নাগরিক সমাজের উদ্বেগ
যুক্তরাষ্ট্রের বহু নাগরিক অধিকার সংগঠন, আইনজীবী সংগঠন এবং শিক্ষাবিদরা ট্রাম্পের বক্তব্যের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। তারা মনে করছেন, এই বক্তব্য জনগণের স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার হরণ করতে পারে। মানবাধিকার সংস্থা ACLU (American Civil Liberties Union) জানিয়েছে, তারা আইনি প্রতিরোধ গড়ে তুলবে যদি এমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়।
রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত প্রতিক্রিয়া
রিপাবলিকান পার্টির অভ্যন্তরে ট্রাম্পপন্থীরা তাঁর এই অবস্থানের পক্ষে থাকলেও, অনেক সিনিয়র রিপাবলিকান নেতা এতে অস্বস্তি প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে, ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতারা একে ‘গণতন্ত্র ধ্বংসের পূর্বাভাস’ বলে অভিহিত করছেন।
ন্যান্সি পেলোসি বলেন,
“ট্রাম্প আবার ক্ষমতায় গেলে, তিনি সংবিধানকে পাশ কাটিয়ে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চান।”
ইতিহাসের আলোকে সেনা মোতায়েনের ঝুঁকি
মার্কিন ইতিহাসে ইনসারেকশন অ্যাক্টের প্রয়োগের নজির বিরল। ১৯৫৭ সালে আর্কানসাসে বর্ণবাদী প্রতিরোধ দমনে, ১৯৯২ সালে লস অ্যাঞ্জেলসে রডনি কিং-এর ঘটনার পর সহিংসতা নিয়ন্ত্রণে এবং ২০০৫ সালে হারিকেন ক্যাটরিনার সময় একাধিকবার আইনটি কার্যকর হয়েছিল।
তবে সবক্ষেত্রেই ব্যবহারের পেছনে ছিল মানবিক বা জরুরি প্রেক্ষাপট। রাজনৈতিক স্বার্থে সেনা মোতায়েন কখনোই ঘটেনি—এটাই ছিল আমেরিকান ঐতিহ্য।
উপসংহার: গণতন্ত্রের জন্য হুমকি না আত্মরক্ষা?
ট্রাম্পের সেনা মোতায়েনের এই প্রচারণা মার্কিন রাজনীতিতে এক নতুন উত্তেজনার জন্ম দিয়েছে। তার কথায় যুক্তরাষ্ট্রকে ‘উদ্ধার’ করার কথা শোনা গেলেও, সেই উদ্ধারের পেছনে লুকিয়ে থাকতে পারে সেনাশাসনের হুমকি।
বিশ্লেষকরা বলছেন, এই ধরনের বক্তব্য শুধু ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণাকেই জোরালো করে না, বরং যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র, সংবিধান এবং নাগরিক অধিকারকে এক পরীক্ষার মুখে ফেলে। শেষ পর্যন্ত ভোটারদের সিদ্ধান্তই নির্ধারণ করবে, তারা আইন ও শৃঙ্খলা চায়, নাকি ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর ভিত্তি করে গঠিত একটি গণতান্ত্রিক সমাজ।
এই প্রতিবেদনটি মার্কিন রাজনৈতিক পটভূমির এক গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ সংকেত বহন করে। ২০২৪-২৫ এর নির্বাচনী প্রেক্ষাপটে ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই উদ্যোগ কেবল একটি রাজনৈতিক কৌশল নয়, বরং গণতন্ত্রের ভবিষ্যত নিয়েও প্রশ্ন তুলছে। ট্রাম্প যদি বাস্তবেই সেনা মোতায়েনের মতো সিদ্ধান্তে অটল থাকেন, তাহলে আমেরিকার রাজনীতি এক ভয়াবহ মোড়ে মোড় নিতে পারে
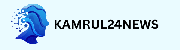

.png)




